
আক্ষরিকভাবে ধরলে আদিবাসী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ভূমিপুত্র। অর্থাৎ ভূমির আদি বাসিন্দা। যদিও বাংলাদেশ সরকার কখনোই কাগজে-কলমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি সরকার আদিবাসী শব্দটি গ্রহণও করেননি। যাদেরকে প্রচলিত সমাজে আদিবাসী বলা হয় তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে বলা হয়েছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। বিগত হাসিনা সরকারের আমলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে জানিয়েছে যে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে যেন প্রচার করার সময় গণমাধ্যমে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার না করে। ২০১১ সালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি ঢাকার বিদেশি কূটনৈতিক মিশনসমূহকে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে যেন আধিবাসী হিসাবে অভিহিত না করে।
এখানে একটি প্রশ্ন আসে তা হলো, তাহলে বাংলা জনপদের আদিমানুষ কারা। বাংলা শব্দের প্রকৃত অর্থ জানা না গেলেও ধারণা করা হয় যে, খ্রিষ্ট জন্মের এক হাজার বছর আগে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে বঙ বা বঙ্গ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলা শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষার বোঙ্গা শব্দটি থেকে এসেছে। বোঙ্গা শব্দটির অষ্ট্রিকদের দেবতার নাম, যা হলো সূর্য। অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠী সূর্যকে বোঙ্গা দেবতা হিসাবে আখ্যা দিত। মহাভারত ও পুরাণ মতে বঙ্গ শব্দটি এসেছে পৌরাণিক রাজা বলির পুত্রের নামানুসারে। বলির পুত্র বঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে পুরাণে বর্ণিত আছে। সংস্কৃত ভাষার বিবিধ গ্রন্থ থেকে বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।
বাংলা জনপদে মুøাদের আগমন ও তাদের বসতি বিন্যেসে যা জানা যায়, মুøারা বাংলা জনপদে বসতি স্থাপন করে খ্রিষ্ট জন্মের দুই হাজার বছর আগে। এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটিত না হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও উৎখননের ভিত্তিতে ভারতের বিহার ও রাচিতে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে ধারণা করা হয় মুøারা বাংলা জনপদের প্রাচীন জাতি। তবে অষ্ট্রিক সাঁওতালদের আগমন এ জনপদে বহু শতাব্দী আগে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মুন্ডা জনগোষ্ঠীর মতো বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানব গোষ্ঠী। এই দুই জনগোষ্ঠী নব্য প্রাস্তর যুগের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বসবাসরত বিশেষ সংস্কৃতির মুন্ডারা খুলনা জেলার কয়রা ডুমুরিয়া উপজেলায়, সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা ও তালা উপজেলায় বসতি গড়ে তুলে। জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে এদেরকে ভারতের ছোট নাগপুরের বৃহৎ দ্রাবিঢ় উপজাতি হিসাবে অনেকেই উল্লেখ করেন। তবে প্রকৃতার্থে এদের বাংলাদেশের মৌলভীবাজার অঞ্চলের বসবাসরত মুন্ডাদের সাথে দৈহিক ও কাঠামোগত মিল রয়েছে। তাতে বিশেষ করে তাদের দৈহিক কাঠামোগত বিন্যেস, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং জেনেটিক ডেরিফের কারণে দ্রাবিঢ় জাতি থেকে মুন্ডারা ভিন্ন বলে মনে হয়। ঐতিহাসিক যুগে এসে প্রথম বঙ্গজ জাতিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়, দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের সাথে আসা গ্রিক ঐতিহাসিকদের লেখায়।
তাদের লেখায় উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ব ভারতীয় শক্তিশালী রাজ্যের কথা। গ্রিক ও অন্যান্য ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ব ভারতে ছোট ছোট বেশ কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। তাদের লেখা গ্রন্থে উল্লেখ আছে এমন রাষ্ট্রগুলোর নাম হলো, গৌড়, বঙ্গ, হরিকেল, চন্দ্রদ্ধীপ, বঙালাবাদ, পুন্ড্র, বরেন্দ্রীয়, দক্ষিণারাঢ়, উত্তর রাধা মন্ডল, তাম্রলিপি, পুন্ড্রবর্ধন, সুবর্ণতিথি, কঙ্কাগ্রামভুক্তসহ মেঘনা অববাহিকার কয়েকটি রাজ্য। এসব রাজ্য বৃহৎ বঙ্গের রাজনৈতিক বিকাশধারা, এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে পুন্ড্র রাজ্যের তাম্রলিপি ছিল একটি আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্রবন্দর। অর্থাৎ আর্য সভ্যতার পাশাপশি এবং আর্যদের আগমনের আগেই এই বঙ্গভূমিতে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট রাজ্য।
মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ এবং ভীমসেনা বঙ্গরাজ্যগুলো জয় করে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। রাজ্যগুলোর খ্যাতি ও বিকাশ এমনই ছিল যে, এগুলো জয় করতে আর্যবর্তের ঐশ্বরিক বীরেরা এসেছিল। বাংলা পিডিয়া থেকে জানা যায়, বাঙালি বা বাঙালি জাতি একটি সংকর জাতি। এরা দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসরত আদিমতম মানব গোষ্ঠী। তবে ধারণা করা হয় যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আর্য অনার্য জাতির সংমিশ্রণের বাঙালি জাতির সৃষ্টি। পরবর্তী সময়ে এসে অষ্ট্রিক ও নিগ্রোটো জাতির মানুষ এসে মিশেছে এই জাতি গোষ্ঠীর সাথে। আর্যরা ভারত বর্ষের অধিবাসী নন। তারা এসেছে বাহির থেকে। তাহলে অনার্য কারা? বর্তমানে বাংলা জনপদে বসবাসরত মানুষগুলো থেকে কীভাবে অনার্য পৃথক করা যাবে? বাংলা শব্দ বা লিপির উৎপত্তি প্রায় ১৫০০ বছর আগে। ব্রাহ্মীলিপি ও সিদ্ধম লিপি থেকে। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় বাঙলা ভাষার প্রচলন শুরু হয় দেড় হাজার বছর আগে।
নৃ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, বাঙালি জাতি একটি মিশ্রিত জাতি। তবে তারা এ অঞ্চলের আদিমতম মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। নৃ-তাত্ত্বিকদের মতে, পৃথিবীর বহুজাতি এই জনপদে প্রবেশ করেছে আবার বেরিয়ে গেছে। তবে পেছনে রেখে গেছে তার অকাট্য প্রমাণ। বৃহত্তর বাঙালি জাতির রক্তে মিশে আছে বিচিত্র সব নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব। দীর্ঘকাল বিভিন্নজন ও কোমের বিভক্ত হয়ে আদি মানুষেরা বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছে। শতকের পর শতকব্যাপী বছর ধরে। জাতিতাত্ত্বিক নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর চারটি প্রধান নরগোষ্ঠীর প্রতিটির কোনো না কোনো শাখার আগমন ঘটেছে বাংলায়। এই চারটি নরগোষ্ঠী হলো নিগ্রীয়, মঙ্গোলীয়, ককেশীয় ও অস্ট্রেলীয়। মনে করা হয় যে, প্রাচীন বাংলার জনগুলোর মধ্যে অষ্ট্রিকরাই বেশি।
বাংলার সাঁওতাল, বাশফোড়, রাজবংশী প্রভৃতি আদি আস্ট্রেলীয়দের সাথে সম্পৃক্ত। এই আদি জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরির্বতন ঘটে আর্যদের আগমনের পর। বাংলাদেশের জনপ্রবাহে মঙ্গোলীয় রক্তের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির রক্তে নতুন করে মিশ্রণ ঘটে পারস্য, তুর্কি, শক জাতির আগমনের ফলে। বাঙালির রক্তে বিদেশি মিশ্রণ প্রক্রিয়া ঐতিহাসিকভাবে সুস্পষ্ট। গুপ্ত, সেন, বার্মন, কম্বেজাখ্য, খড়গ, তুর্কি, আফগান, মুঘল, পর্তুগিজ, ইংরেজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি বহিরাগত জাতি বাংলা শাসন করেছে। প্রতিটি জাতি তাদের শাসনকালে রেখে গেছে রক্তের ধারা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই সংকারায়ন আরো বেড়েছে। তাই এককথায় বলা যায় বাঙালি সংকর জাতি। পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী ও লৌকিক দেব-দেবীর সাথে রাজ্যের লোক সংস্কৃতির যোগটা অবিচ্ছেদ্য। যা পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে বিস্তৃত। তবে পূর্ব বাংলায় ৭৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ব বাংলায় বেশি মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে এখানে আদিবাসীদের পূজা অর্চনা সংকোচিত হতে শুরু করে ওই সময়টায়। এসব দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে আযোজিত গ্রামীণ মেলা ও উৎসব এখনো দুই বাংলায় বিদ্যমান। এই মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য ঘূর্ণায়মান হয়। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ রক্ষায় এই উৎসবগুলো গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে।
এই ব্যাখ্যায়মান ধারায় আদি মানুষ কারা বাংলা জনপদে? তা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের কাছে রইল। তবে রাজনৈতিক বিচারে একটি বিষয় উঠে আসে তা হলো, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে তারা আরো বেশি অধিকার পাবে। ২০০৭ সালে পাস হওয়া ইউনাইটেড নেশসন ডিক্লারেশন অব দ্য ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস বা ইউএনডিআরআইপি অনুযায়ী, আদিবাসীদের নিজেদের উন্নয়ন ধারা নিজেরা নির্ধারণ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্য হয়ে উঠবেন। বাংলাদেশের গত সরকার তা দিতে রাজী নন। তাই তারা এই ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করেনি। তবে সময় এসেছে এই জনপদের আদি মানুষ বা অধিবাসী কারা তা নির্ণয় করার।
লেখক: কলামিস্ট
মানবকণ্ঠ/আরএইচটি
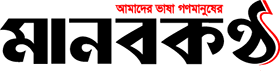





Comments